রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা “ছুটি” গল্প থেকে SAQ প্রশ্ন-উত্তর
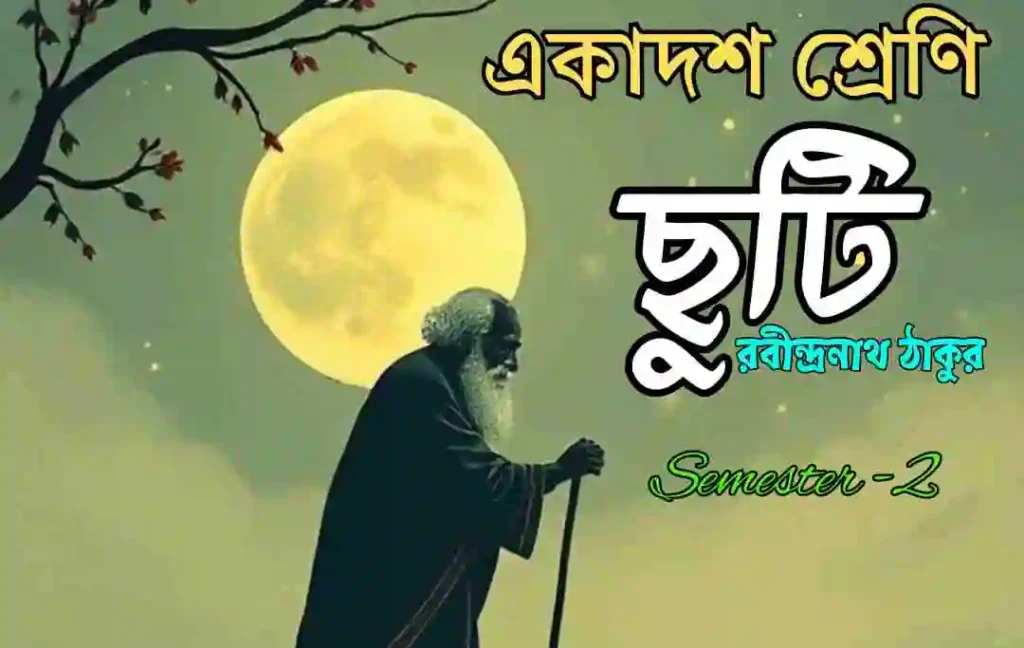
ছুটি -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১. “বিশেষত তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই”- কোন প্রসঙ্গে মন্তব্যটি করা হয়েছে? এমন মন্তব্যের কারণ কী ?
আধুনিক ছোটোগল্পের সার্থক স্রস্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ছুটি’ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ফটিককে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলার জন্য তার মামা বিশ্বস্তুর বাবু তাকে কোলকাতায় নিজের বাড়িতে নিয়ে যান কিন্তু এই অশিক্ষিত গেঁয়ো ছেলেকে নিয়ে অনাবশ্যক পরিবার বৃদ্ধিতে ফটিকের মামি অসন্তুষ্ট হন– এই প্রসঙ্গে লেখক উক্ত মন্তব্যটি করেছেন।
∆ ‘বালাই’ কথার অর্থ হল বালকের অহিত বা অমঙ্গল। এখানে ‘বালাই’ শব্দটি কেবল বিপদ বা অমঙ্গল অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। গল্পকারের বর্ণনা অনুযায়ী তেরো-চৌদ্দ বছরের ছেলেরা পৃথিবীর সবার চোখে বিপদ বা অমঙ্গল -স্বরূপ। এর প্রধান কারণ হল বয়ঃসন্ধি। এই সময় প্রাকৃতিক নিয়মেই তাদের শরীর ও মনের কিছু আকস্মিক অথচ অনিবার্য পরিবর্তন ঘটে । এর ফলে-
1. শিশুর শরীরে যে সৌন্দর্য বা লাবণ্য থাকে তা এই বয়সে আর থাকে না, অর্থাৎ ‘শোভা নাই’।
2. এই বয়সে জ্ঞান পরিপক্ক নয় তাই তারা “কোনো কাজে আসে না”।
3. এই সময়ে তাদের আচরণে শিশুসুলভ সারল্য থাকে না তাই তারা অন্যের হৃদয়ে “স্নেহের উদ্রেক করে না”।
4. তাদের সঙ্গও সুখকর নয় তাই তাও প্রার্থনীয় নয়।
5. এই বয়সে শিশুদের মতো আধো কথা-ন্যাকামি, বড়োদের মতো যুক্তিপূর্ণ কথা-জ্যাঠামি এবং অতিরিক্ত কথা প্রগলভতার নামান্তর।
6. তাদের হঠাৎ দৈহিক বৃদ্ধি বেমানান এবং কুশ্রী স্পর্ধা বলে মনে হয়।
7. এদের কন্ঠস্বরও সহসা মিষ্টতা হারায়, সবার কাছে সেটা যেন তাদের অপরাধ বলে গণ্য হয়। অথচ এসবের জন্য তারা দায়ী নয় কিন্তু মনস্তত্ত্বজ্ঞানহীন মানব এই দায় বলপূর্বক কিশোরের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাকেই দায়ী করে তোলে। এক প্রকার প্রবল বিতৃষ্ণার কারণে এই স্বাভাবিক পরিবর্তনকে তারা মেনে নিতে পারে না। গল্পকারের কথায়- “যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায় কিন্তু এই সময়ে কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়”। তাই তেরো- চৌদ্দ বছরের ছেলে বড়োদের কাছে বালাই ছাড়া আর কিছু নয়। ফটিককে কেন্দ্র করে আলোচিত এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গল্পকার বিশেষ থেকে নির্বিশেষ বিশ্বজনীনতা দান করেছেন।
২. “মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা , এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি”- ছুটির জন্য বক্তার সেই আকুলতার কারন কী ? শেষ পর্যন্ত বক্তা কীভাবে কাঙ্ক্ষিত ছুটি পেয়েছিল ? উডক্তিটির তাৎপর্য আলোচনা করো।
রবীন্দ্রনাথের ‘ছুটি‘ গল্পের ফটিক আদ্যোপান্ত এক প্রকৃতি লালিত বালক। তাঁর রক্তে-মাংসে – অস্থি – মজ্জায় মিশে রয়েছে ঘুড়ি ওড়ানোর বিস্তীর্ণ প্রান্তর, অকর্মণ্যভাবে গান গেয়ে ঘুরে বেড়ানোর প্রশান্ত নদীতীর, সানন্দে সাঁতার দেওয়ার সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী। এই প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই সে শহর কলকাতায় আসে। কিন্তু কলকাতায় আসার আনন্দ তার মুহূর্তেই ম্লান হয়ে যায়। মামার বাড়ির “ভারি মজার” পরিবর্তে মামির অনাদর, প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন শহরের বদ্ধ জীবন, স্কুলে মাষ্টার মশাই-এর শাসন-পীড়ন- কটু বাক্য প্রয়োগ, মামাতো ভাইদের তার সঙ্গে সম্বন্ধ অস্বীকার – ইত্যাদি অবহেলা – উপেক্ষা- উপদ্রবে অতীষ্ট ফটিকের চোখে হয়তো বারংবার অশ্রু ঝরেনি কিন্তু হৃদয়ে ঘটেছে রক্তক্ষরণ। সবার কাছে অপাংক্তেয় জীবনে সে উপলব্ধি করে তার এই অদৃশ্য ক্ষতস্থানের রক্ত মুছিয়ে দিতে পৃথিবীতে একজন মানুষই আছে- সে তার অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা।
হঠাৎ যেন মানবী মা আর প্রকৃতি মায়ের স্নেহক্রোড় তার কাছে নিবীড় আকাঙ্ক্ষার বস্তু হয়ে ওঠে। কিন্তু পুজোর ছুটি এখনও অনেক দূরে। তখন বন্দী জীবনের অসহনীয় অব্যক্ত যন্ত্রনা থেকে মুক্তির প্রার্থনাই হয়ে ওঠে বন্দী ফটিকের একমাত্র বন্দনা এবং এটাই তার মুক্তি-ব্যাকুলতার কারন।
∆ শহরের বন্দী জীবনে ঘরে-বাইরে অবহেলা, অনাদর ও নিগ্রহের শিকার হতে হতে ফটিকের মধ্যে মুক্তি খোঁজার সাহস জাগে। তারপর এক রাত্রে যখন সে শরীরে জ্বরের পূর্বাভাস অনুভব করে তখন সে আর মামীর উপদ্রব হতে চায়নি। মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য বৃষ্টির মধ্যে সে পথে পা বাড়ায়। বিশ্বম্ভর বাবু তাকে খুঁজে না পেয়ে পুলিশে খবর দেয় এবং পুলিশ তাকে ফিরিয়ে আনে। ফটিকের মুক্তি-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বৃষ্টিতে ভিজে তার জ্বর বেড়ে যায়। সে প্রলাপ বকতে শুরু করে। চিকিৎসক বিমর্ষ -চিন্তিত মুখে জানায় “অবস্থা বড়োই খারাপ”। সংবাদ দিয়ে ফটিকের মাকে আনতে পাঠায় বিশ্বম্ভরবাবু। মায়ের উচ্ছ্বসিত রোদন ও অশ্রুপাত ফটিকের তপ্ত ললাট শীতল করতে পারে না। জ্বরের ঘোরেই মায়ের কন্ঠস্বর শুনে সে মাকে তার ছুটির কথা এবং বাড়ি যাওয়ার কথা জানায়। শেষ পর্যন্ত মাকে শিয়রে রেখেই সে পুজোর ছুটির আগেই জীবন থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি অর্থাৎ চির প্রশান্তির দেশে যাত্রা করে। এভাবেই বক্তা অর্থাৎ ফটিক শেষ পর্যন্ত তার কাঙ্ক্ষিত মুক্তি বা ছুটি পেয়েছিল।
∆ স্নেহ ভালোবাসার রসসিঞ্জনে মানব হৃদয় সঙ্গীবিত ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে অনাদর-অবহেলা সেই জীবনীশক্তিকে নিঃশেষ করে। তাকে শুষ্ক রুক্ষ মরুতে পরিণত করে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। তখন মানুষ ছুটি খোঁজে- নিত্যদিনের কাজকর্ম বা স্কুল- কলেজ থেকে ছুটি নয়, তা জীবন থেকে ছুটি। কারণ ” চাইনা বাঁচতে আমি প্রেমহীন হাজার বছর।” আর এই সত্যই ‘ছুটি’ গল্পের ‘ছুটি’ শব্দটিকে নিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছে । তবে গল্পে লেখক খুব সন্তর্পণে ফটিকের জীবনদীপ নির্বাপিত করতে চেয়েছেন। গল্পে কোথাও সরাসরি ফটিকের মৃত্যুর কথা বলা হয়নি কিন্তু তার জ্বরে অচেতন হওয়া, বিশ্বম্ভর বাবুর রুমালে চোখ মোছা, ফটিকের প্রলাপ বকা, চিকিৎসকের বিমর্ষ মন্তব্য -“অবস্থা বড়োই খারাপ”, প্রলাপের মধ্যে ফটিকের জ্বর মাপা এবং অন্ত না পাওয়া, মায়ের উচ্চৈস্বরে উচ্ছ্বসিত শোক প্রকাশ ইত্যাদি ঘটনা, তার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। এভাবেই ফটিক স্কুলের পূজোর ছুটির আগেই জীবন থেকে কাঙ্ক্ষিত ছুটি নেয় । অথচ এ ছুটির অর্থ বোঝেনা বালক ফটিক। একদিন সে নিজেই ছুটি নিয়ে মায়ের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। সেই আকাঙ্ক্ষা তার অবচেতন মনে বাসা বেঁধেছিল। ঘোরের মধ্যে তাই মায়ের কন্ঠস্বর শুনে সে বাড়ি যাওয়ার কথা বলে। এই ছুটি এবং বাড়ি যাওয়ার অর্থ প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন, অনাদর- অবহেলার বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে চিরপ্রশান্তির দেশে যাত্রা ।
